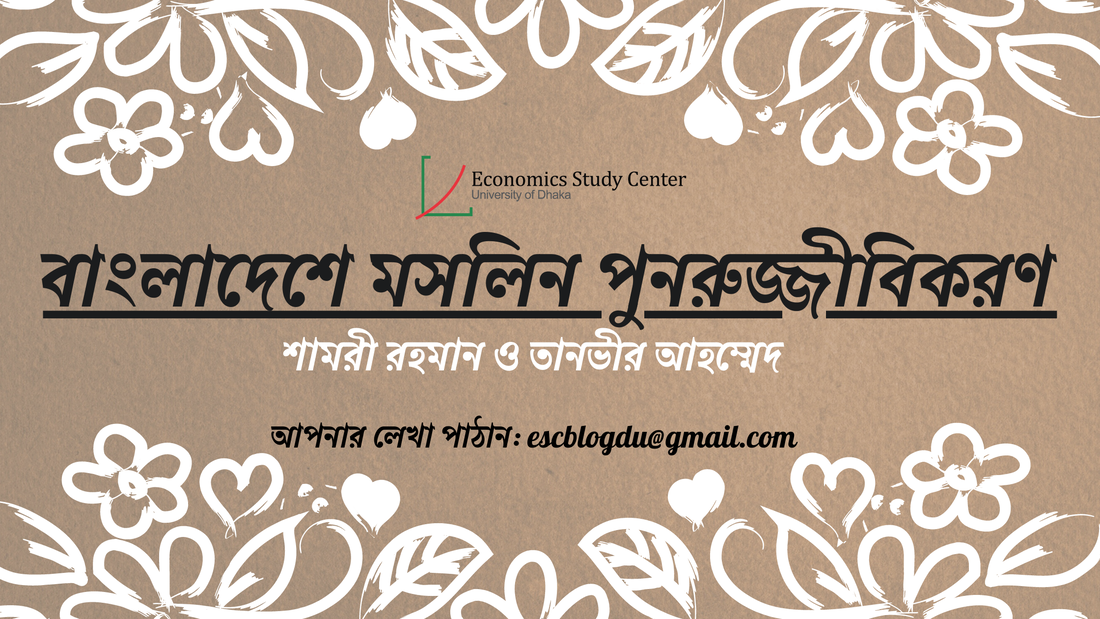ECONOMICS STUDY CENTER, UNIVERSITY OF DHAKA
|
শামরী রহমান, তানভীর আহম্মেদ ডিজাইন: ফারহা তাসনীম “চরকায় সম্পদ, চরকায় অন্ন, বাংলার চরকায় ঝলকায় স্বর্ণ! বাংলার মসলিন বোগদাদ রোম চীন কাঞ্চন-তৌলেই কিনতেন একদিন।” সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতা “চরকার গানের” এই চরণগুলো যে কিংবদন্তী ঢাকাই মসলিনের নিয়ে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। তবে ‘মসলিন’ শব্দের উৎপত্তির উৎস অস্পষ্ট। খুব সম্ভবত ইউরোপীয়দের মসুল থেকে আমদানিকৃত কাপড় ও প্রাচ্যের দেশগুলোর মসুল হয়ে আনা কাপড়ের সুত্র ধরেই এই মসলিন নামকরণ। মসলিনের প্রাচীন নাম “গঙ্গাপট্টাহি”। মসলিন সব তুলা থেকে তৈরি করা যায় না, উৎকৃষ্ট মানের মসলিনের জন্য দরকার হয় বিশেষ ধরনের তুলা যার নাম ‘ফুটি কার্পাস’। এই ‘ফুটি কার্পাস’ আবার সব জায়গা পাওয়া যায় না,তবে ইতিহাস ঘেটে জানা যায় উৎকৃষ্টমানের মসলিন তৈরির জন্য প্রসিদ্ধ কয়েকটি এলাকা ছিল- বর্তমান ঢাকা জেলার ঢাকা ও ধামরাই, গাজীপুর জেলার তিতাবদি, নারায়ণগঞ্জ জেলার সোনারগাঁও এবং কিশোরগঞ্জ জেলার জঙ্গলবাড়ি ও বাজিতপুর।বিভিন্ন তথ্যসূত্র থেকে মোট ২৮ প্রকারের মসলিন কাপড় উৎপাদনের কথা জানা যায়, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হল- মলমল (সূক্ষ্মতম বস্ত্র), ঝুনা (স্থানীয় নর্তকীদের ব্যবহূত বস্ত্র),আবি-রাওয়ান (প্রবহমান পানির তুল্য বস্ত্র), শবনম (ভোরের শিশির),বদন-খাস (বিশেষ ধরনের বস্ত্র), জামদানি (নকশা আঁকা) ইত্যাদি। বর্তমানে যেটা জামদানী হিসেবে পরিচিত তখন এটি ছিল নকশা করা নিম্নমানের মসলিন আর সবচেয়ে সূক্ষ্ম মসলিনের নাম ছিল “মলমল” বা “মলমল খাস”। এই ব্লগে থাকছে মসলিনের পরিচয়, ব্যবহার, ইতিহাস উপাখ্যান, বিলুপ্তি ও এর পুনঃজন্ম। এছাড়াও বর্তমানে নতুন করে মসলিনের উৎপাদন ও বাংলাদেশের অর্থনীতিতে এর সুদূর প্রসারি ভূমিকা নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা। মসলিনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাসঃ মসলিন হাজার বছরেরও পুরনো। মসলিন নিয়ে অনেক কিংবদন্তি প্রচলিত আছে। বার্ডউড তাঁর “ইন্ডাস্ট্রিয়াল আর্টস অব ইন্ডিয়া” গ্রন্থে মসলিনকে অভিহিত করেন সোলেমানের পর্দার মতো লাবণ্যময় ও মনুসংহিতার চাইতে প্রাচীনতর বলে । “বাংলাদেশ থেকে সুদূর পশ্চিমে ঢাকার মসলিন রপ্তানি হতো।“ [বাংলাদেশের উৎপত্তি ও বিকাশ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, পৃ ২৭-২৮] এই কথার যথার্থতা পাওয়া যায় “পেরিপ্লাস অব ইরিত্রিয়ান সী” নামের গ্রন্থ থেকে। এখান থেকে জানা যায় খ্রিস্টীয় প্রথম শতাব্দীতে আরব বণিকরা হাতির দাঁত, কচ্ছপের খোল এবং গন্ডারের শিংয়ের বিনিময়ে ভারতীয় বণিকদের কাছ থেকে মসলিনসহ বিভিন্ন ধরনের কাপড় কিনতেন এবং সেগুলোকে লোহিত সাগরের ইথিওপিয়া ও মিশরে নিয়ে আসতেন। তখন মসলিনের ব্যাপ্তি ছিল রোমান সাম্রাজ্যসহ পুরো ইউরোপ জুড়ে। মিশরের মমি সংরক্ষণের কৌশল নিয়ে গবেষণার এক পর্যায়ে সামনে আসে চমকপ্রদ তথ্য, জানা যায় মমি তৈরিতে এক অতি সূক্ষ্ম কাপড় ব্যবহার করা হতো যেটা ভারতবর্ষ থেকে যেত। মমি সংরক্ষণে মসলিনের এই ব্যবহারের কথা পন্ডিত জওহরলাল নেহেরু তার “গ্লিম্পেসস অফ ওয়ার্ল্ড হিস্ট্রি” বইটিতেও উল্লেখ করেছেন। রোমান পণ্ডিত গ্লিনি গঙ্গেয় মসলিন নামে পরিচিত ঢাকার মসলিনের ভূয়সী প্রশংসা করেন। মসলিনের আরও উল্লেখ পাওয়া যায় টলেমির ভূগোল এবং প্রাচীন চীনা পরিব্রাজকদের বর্ণনায়। মরক্কোর বিখ্যাত পর্যটক ইবনে বতুতা তার সোনারগাঁও সফরকালে মসলিনের উৎপাদন দেখে চমৎকৃত হয়ে মন্তব্য করেন-”এমন উন্নতমানের বস্ত্র হয়তো সারা দুনিয়ায় আর কোথাও পাওয়া সম্ভব নয়।” শুধু ইবনে বতুতা নয় মসলিনের সূক্ষ্ম বুননের বন্দনা শোনা যায় মাহুয়ান,রলফ ফিচ,ডুয়ার্টে বারবোসা এবং স্ট্যাভোরিনাস এর মতো নানা সময়ের বিখ্যাত সব পর্যটকদের মুখে। মসলিনের ব্যাপক প্রসার ঘটে মোঘল আমলে। মোঘল সম্রাট ও অভিজাতরদের পৃষ্ঠপোষকতার কারনে সে সময় মসলিন শিল্প ছিল স্বয়ংসম্পূর্ণ।মুলত মুঘল আমলে বাংলার রাজধানী ঢাকায় স্থানান্তরিত হওয়ার পর থেকে এটি ভারতবর্ষে ছাড়িয়ে বিদেশি ক্রেতাদেরকেও আকৃষ্ট করে। মুঘল আমলকে ঢাকাই মসলিনের স্বর্ণযুগ বলা হয়। মোঘল রাজদরবারে ব্যবহারের জন্য সংগ্রহ করা হতো বিপুল পরিমান মসলিন কাপড় । সম্রাটদের জন্য সংগৃহীত কাপড়ের নাম ছিল মলবুল খাস এবং নওয়াবদের জন্য সংগৃহীত কাপড়ের নাম ছিল সরকার-ই-আলা। সে সময় সম্রাট ও উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের ব্যবহারের জন্য তৈরী মসলিন কাপড়ের বুনন তদারকির জন্য দারোগা বা দারোগা-ই-মলবুস খাস উপাধিধারী একজন কর্মকর্তা নিয়োগ করা হতো। মলমল (বা মলবুস খাস ও সরকার-ই-আলা) ব্যতীত অন্যান্য মসলিন বস্ত্র ব্যবসায়ীরা রপ্তানি করত। স্থানীয় লোকেরাও কিছু কিছু মসলিন বস্ত্র ব্যবহার করত।মসলিন কাপড় তৈরি হতো আরও দুটি নামে-”খাসসা ও শবনম”। ‘খাসসা’ একটি ফার্সি শব্দ হলেও ইংরেজরা এ জাতীয় মসলিনকে বলতো ‘কুষা’। সোনারগাঁওয়ে খাসসা ব্যাপকভাবে তৈরি হতো বলে জানা যায়। চিত্রঃ নেপোলিয়ানের প্রথম স্ত্রীর অত্যান্ত প্রিয় পরিধেয় ছিল ঢাকাই মসলিন সূত্রঃ প্রাচীন যে বস্ত্রের বুনন কৌশল কেউ জানে না! | The Business Standard একসময় যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞ থেকে নেপোলিয়নের স্ত্রী জোসেফিন হয়ে আওরঙ্গজেবের মেয়ে জেবুন্নেসা আর ফ্রান্সের রানি মেরি অ্যান্টোনিয়েটের অঙ্গে সোভা পেয়েছে এই মসলিন কাপড়। মোঘল সম্রাজ্ঞী নূরজাহান মসলিনের বিশেষ কদর করতেন। মসলিন শুধু ভারতীয় উপমহাদেশে নয়, ইউরোপীয় নারীদের গায়েও শোভা পেত। ইতিহাস বলে, সম্রাট নেপোলিয়নের পত্নী সম্রাজ্ঞী জোসেফিন তার অন্দরমহলে মসলিনের তৈরি পর্দা ব্যবহার করতেন। গ্রীক ঐতিহাসিক মেগাস্থিনিস এর কথাতেও অতীতে মসলিন ব্যবহারের নজির দেখা যায়- “ভারতীয়রা সোনার কাজ করা উৎকৃষ্ট মানের মসলিনের কাপড় পরত, কতগুলোতে ভরা ফুলের নকশা ছিল।” -মেগাস্থিনিস, গ্রিক ঐতিহাসিক, ভারতীয় সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের দরবারের প্রতিনিধি, খ্রিষ্টাব্দ ৩৫০-২৯০  চিত্রঃ নবাব টিপু সুলতানের ব্যবহৃত মসলিন সূত্রঃ মসলিনের খোঁজে | প্রথম আলো চিত্রঃ নবাব টিপু সুলতানের ব্যবহৃত মসলিন সূত্রঃ মসলিনের খোঁজে | প্রথম আলো হাজার বছরের পুরোনো ঐতিহ্য, পৃথিবীর বিস্ময় এই মসলিন কাপড় তৈরি নিয়ে নানা লোকশ্রুতি রয়েছে। রোমানরা মসলিনকে বলত “বাতাসে গেরো দিয়ে তৈরি করা কাপড়।” আর ব্রিটিশরা ত ধরেই নিয়েছিল যে, এই কাজ মানুষের দ্বারা সম্ভব নয়, এ নিশ্চয় পরীদের কাজ। ব্রিটিশদের এই ধারণার যথার্থতা পাওয়া যায় ওয়াটসন এর উক্তিতে- “স্বীকার করতে হয় ঢাকার “বোনা বাতাস” সবচেয়ে উৎকৃষ্ট।“ -জন ফোর্বস ওয়াটসন, লন্ডনে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ভারত কার্যালয়ের প্রতিবেদক, ১৮২১-১৮৯২ কয়েক গজ মসলিন কাপড় ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দেয়া যেত বলে জনসাধারণ একে “হাওয়ার কাপড়ও” বলতো। মসলিন নিয়ে ডাচ বণিক, উইলিয়াম বোল্টসের অনেকগুলো মজার গল্প রয়েছে। সেগুলোর একটা হল- “আলীবর্দি খাঁ একবার এক গরুর মালিককে শাস্তি দেন কারন তার গরু শিশিরে ভেজা ঘাসের সাথে একাকার হয়ে থাকা মসলিন কাপড় খেয়ে ফেলেছিল।“ মসলিনের এই সূক্ষ্মতার বিবরণ পাওয়া যায় ফরাসি রত্ন ব্যবসায়ী তাভের্নিয়ের মাধ্যমে- “মনে হয়, একটা মাকড়সার জাল...এতই সূক্ষ্ম যে হাতে ধরলে প্রায় বোঝা যায় না, কী ধরেছি হাতে।“ -জাঁ-বাপতিস্ত তাভের্নিয়ে, সপ্তদশ শতকের ফরাসি রত্ন ব্যবসায়ী ও পরিব্রাজক, ১৬০৫-১৬৮৯ এটাও কথিত আছে যে, বাংলার ঢাকাই মসলিন এত সূক্ষ্ম যে বিশ ইয়ার্ডের একেকটি মসলিন বস্ত্রকে দেশলাই বাক্সে ভাঁজ করে রাখা যায়। মসলিনের বিলুপ্তি ও পুনঃজন্ম- মসলিনের বিলুপ্তির অনেকগুলো কারন আছে । ইংরেজরা বুঝতে পেরেছিল তাদের তৈরি কাপড়ের একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী এই মসলিন কাপড় তাই একে বিলুপ্ত করার অভিপ্রায়ে মসলিনের শুল্ক উচ্চ করে দেওয়া, তাতিদের যথাযথ সম্মান ও পারিশ্রমিক না দেওয়া ও মসলিন তাঁতিদের আঙুল কেটে দেওয়ার মতো ঘটনা ঘটিয়েছে তারা। এত প্রতিকূলতায় আস্তে আস্তে বন্ধ হয়ে যায় মসলিন বুনোন,সেইসঙ্গে বিলীন হয়ে যায় বাংলার হাজার বছরের ঐতিহ্যের মসলিন। মুঘল বাদশাহ, নওয়াব এবং উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের পৃষ্ঠপোষকতার অভাবও ঢাকাই মসলিন শিল্পের অবনতির অন্যতম কারণ তবে এর চূড়ান্ত বিলুপ্তির কারণ হিসেবে ধরা হয় ইউরোপের ‘শিল্প বিপ্লব’ এবং আধুনিক বাষ্পশক্তি ও যন্ত্রপাতির আবিষ্কার। ইংল্যান্ডের শিল্প-কারখানায় উৎপাদিত সস্তা দামের পণ্যের সাথে প্রতিযোগিতায় হেরে যায় ঢাকাই মসলিন। কিন্তু আশার খবর এই যে, ২০১৪ সালের অক্টোবরে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় পরিদর্শনের সময় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মসলিনের ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনার কথা বলেন। প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনার পরিপ্রেক্ষিতে শুরু হয় মসলিন তৈরির প্রযুক্তি উদ্ভাবনের জন্য গবেষণা, তৈরি করা হয় কমিটি যার নেতৃত্ব দেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক মো. মনজুর হোসেন তাছাড়া মসলিন পুনরুজ্জীবনের এই রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতায় যেসকল গবেষক অবদান রেখছেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকজন হল- বাংলাদেশে তাঁত বোর্ডের চেয়ারম্যান,বাংলাদেশ টেক্সটাইল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শাহ আলীমুজ্জামান, বাংলাদেশ তুলা উন্নয়ন বোর্ডের অতিরিক্ত পরিচালক মো.আখতারুজ্জামান, বিটিএমসি ঢাকার মহাব্যবস্থাপক মাহবুব-উল-আলম, বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডের উপমহাব্যবস্থাপক এ এস এম গোলাম মোস্তফা ও তাঁত বোর্ডের জ্যেষ্ঠ ইনস্ট্রাক্টর মো. মঞ্জুরুল ইসলাম। পরবর্তীতে গবেষণা কাজকে ত্বরান্বিত করতে আরও ৭ জনকে যুক্ত করা হয়। মসলিন পুনরুদ্ধারের এই কাজ সম্পন্ন করার জন্য হাতে নেওয়া হয় “বাংলাদেশের সোনালি ঐতিহ্য মসলিন সুতা তৈরির প্রযুক্তি ও মসলিন কাপড় পুনরুদ্ধার (প্রথম পর্যায়)” শীর্ষক প্রকল্পটি এবং এর ব্যয় ধরা হয় ১৪ কোটি টাকা।
পাড়ি দিতে হয়েছে তুলার গাছ (ফুটি কার্পাস) খুঁজে বের করা, ঢাকাই মসলিনের নমুনা সংগ্রহ ও তার ডিএনএ সিকুয়েন্স বের করা, সুতা কাটার জন্য দক্ষ তাঁত খুজে বের করা ও নতুন করে চরকা তৈরির মতো ব্যাপক শ্রমসাদ্ধ ধাপগুলো। “তবে প্রকল্পটির একটি চমকপ্রদ দিক হল এটি পুনরুদ্ধারে সর্বসাধারণের সরব উপস্থিতি। কে নেই সেখানে মন্ত্রী-প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে সোশ্যাল মিডিয়া,পত্র-পত্রিকা ও সংবাদের মাধ্যম যে যেভাবে পেরেছে অবদান রেখেছে মসলিন পুনরুদ্ধারে। প্রকল্পটির আরেকটি ইতিবাচক দিক হল সরকারি সম্পদ ব্যবহারে মিতব্যয়িতা। প্রকল্পের জন্য বরাদ্দ ছিল ১৪ কোটি ১০ লাখ টাকা যার মধ্যে ছয় বছরে (২০১৪-২০২০) খরচ হয়েছে সোয়া চার কোটি টাকা অব্যবহিত প্রায় ৭০% টাকা সরকারি খাতে ফেরত দেওয়া হয়েছে। মসলিন গবেষকরা জানিয়েছেন, ৭০০ কাউন্ট মিহি সুতোয় বুনোনো মসলিনের সুতা চুলের থেকেও বেশি সূক্ষ্ম ছিল। সর্বোচ্চ ১২০০ কাউন্টের মসলিনের কথাও জানা যায়। ৫০০ কাউন্টের উন্নত মসলিন তৈরির স্বীকৃতি হিসেবে বাংলাদেশ পেয়েছে মসলিনের ‘জি আই বা জিওগ্রাফিকাল ইন্ডিকেশন’, অর্থাৎ বাংলাদেশ এখন নিজেদেরকে বিশ্বে মসলিনের উৎপাদক ও এর বাণিজ্যিকীকরনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারবে। অর্থনৈতিক গুরুত্ব- জেমস টেলরের লেখায় জানা যায়, ১৭৮৭ সালে ঢাকা থেকে যে পরিমাণ মসলিন ইংল্যান্ডে রপ্তানি করা হয়েছিল, তার মূল্য ছিল তৎকালীন ৩০ লাখ টাকা। ১৮১৭ সালে এই রপ্তানি পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যায়। প্রকল্প সংশ্লিষ্টরা জানতে পেরেছেন, ১৭৪৭ সালে ঢাকা থেকে যে পরিমাণ মসলিন রপ্তানি এবং সম্রাট-নওয়াবদের জন্য সংগৃহীত হয়, তার মূল্য ছিল তখনকার সময়ের ২৮ লাখ ৫০ হাজার টাকা। পলাশীর যুদ্ধের পর ঢাকার মসলিন শিল্পে বিপর্যয় নেমে আসে এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে ঢাকার মসলিনের রপ্তানির পরিমাণ ১৭৪৭ সালের চেয়ে অর্ধেকে নেমে আসে। বিবিসির এক প্রতিবেদনে গবেষক সাইফুল ইসলাম তার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে বলেন- “ভারতের একটি গ্রাম মসলিনের নামে বছরে ২৫ কোটি টাকার কাপড় বিক্রি করেছে। ভারত খাদি মসলিন হিসেবে বছরে প্রায় ৮০০ কোটি টাকার ব্যবসা করে। কিন্তু এগুলোকে সব বলা হয় বেঙ্গল মসলিন। তাহলে নিশ্চয়ই মসলিনের বাজার আছে।” মসলিন কাপড় এখনো ইউরোপের বিভিন্ন দেশে জনপ্রিয় বলে উল্লেখ করেছন মি: ইসলাম। তবে এটা কোনদিন সাধারণ মানুষের জন্য জনপ্রিয় হবে না বলে তিনি উল্লেখ করেন। চিত্রঃ নারায়ণগঞ্জে ঢাকাই মসলিনের কারখানায় ঐতিহ্যবাহী মসলিনের পোশাক তৈরির জন্য শ্রমিকদের তুলা থেকে সুতো কাটা দেখছেন আইয়ুব আলী সূত্রঃ Textile hub Bangladesh revives muslin, the forgotten elite fabric | Fashion Industry News | Al Jazeera মসলিনের এই পুনরুজ্জীবন নিঃসন্দেহে বাংলাদেশের জন্য এক বিশাল মাইলফলক। এর পুনরুজ্জীবনের মধ্য দিয়ে দেশের জন্য নানামুখী সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচিত হতে চলেছে বলে আশা করা যায়। ইতোমধ্যেই, প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জে তৈরি হয়েছে মসলিনের কারখানা যেখানে পুরো উদ্যমের সাথে চলছে মসলিন উৎপাদন ও বাণিজ্যিকীকরণের কাজ। মূলত একটি পরিত্যক্ত জুট ফাইবার মিলকে মসলিন কারখানা হিসেবে বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। সেখানে মোট ১৮টি তাঁতে ১২৫ জন প্রশিক্ষিত তাঁতী প্রাচীন পদ্ধতিতে ৫০ টি মসলিন শাড়ি তৈরির লক্ষ্যে কাজ করছেন। পরিকল্পনা অনুযায়ী, মসলিনের বাণিজ্যিকীকরণের ক্ষেত্রে প্রাচীন ও আধুনিক উভয় পন্থাই অবলম্বন করা হবে। তবে এর উৎপাদনে হস্তশিল্পের প্রাধান্য থাকবে কারণ তা না হলে মসলিনের প্রধান স্বকীয়তা অর্থাৎ এর “স্পর্শসুখানুভূতি” বজায় রাখা সম্ভব হবে না। প্রাচীন পন্থায় তৈরি মসলিন হবে উচ্চমূল্যের যা বিদেশে রপ্তানি করা হবে। এখানে সংযোজন করা প্রয়োজন, প্রাথমিক পর্যায়ে একটি মসলিন তৈরি করতে সময় লেগেছে ছয় মাস এবং ব্যয় হয়েছে ৩ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা। বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদন করলেও এর দাম ১ লক্ষ টাকার নিচে হবে না। অর্থাৎ এই মসলিন থেকে বেশ সম্ভাবনাময় রপ্তানি আয় হবে বলে ধারণা করা যায়। এই সম্ভাবনা দেশী ও বিদেশী বিনিয়োগকারীদের আকৃষ্ট করবে মসলিন বাণিজ্যিকীকরণে। ফলে মসলিনকে ঘিরে পুনরায় কর্মসংস্থান হবে কর্মহারা তাঁতীদের। বুননকৌশলে প্রশিক্ষিত করার মাধ্যমে কিছুসংখ্যক বেকার জনগোষ্ঠীকে এই কাজের সাথে যুক্ত করাও সম্ভব হবে। গবেষকরা জানিয়েছেন, মসলিনের বিলিয়ন ডলারের মার্কেট রয়েছে ইতোমধ্যেই। গাজীপুরে বর্তমান কারখানাগুলোর মতই একসময় মসলিন ইন্ডাস্ট্রি গড়ে তোলা হবে। সেই সাথে বাণিজ্যিকভাবেই করা হবে ফুটি কার্পাস চাষ। এভাবে, সমগ্র জিডিপিতেই মসলিন শিল্প বা বাণিজ্য বেশ ইতিবাচক প্রভাব রাখবে বলে আশা রাখা যায়। ঐতিহ্য এবং অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির অনবদ্য মেলবন্ধন ছিল এই মসলিন। মোঘল রাজশক্তির পতন, ব্রিটিশ শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতার অভাব, ইংল্যান্ডের শিল্প বিপ্লব সহ আরও নানা কারণে হারিয়ে গেলেও মসলিনের আভিজাত্যের গল্প নানাভাবে এসেছে আমাদের কাছে। এখনও সে আভিজাত্যের কদর রয়েছে সারাবিশ্বে। তাই মসলিনকে নিয়ে যে সম্ভাবনার কথা বলা হচ্ছে তা কোনভাবেই অলীক নয়। গল্পে শোনা মসলিনকে এবার কেবল ভালবেসে গায়ে জড়াবার পালা। ফিরে যাবার পালা আরও একবার আপন সত্ত্বায়। মসলিনকে ঘিরে আরও একবার আপন পায়ে দাঁড়ানোর গল্প রচনার পথে বাংলাদেশ। তবে, বাণিজ্যিক সম্ভাবনার চেয়ে মসলিনকে ইতিহাস, ঐতিহ্য এবং আভিজাত্যের প্রতীক হিসেবেই দেখছেন আয়োজকরা। তথ্যসূত্র-
0 Comments
Leave a Reply. |
Send your articles to: |