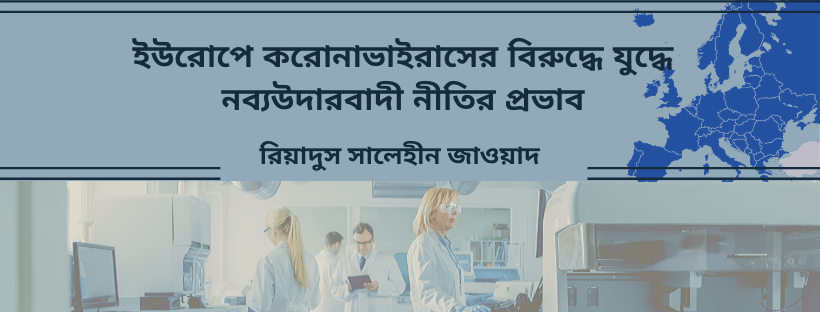ECONOMICS STUDY CENTER, UNIVERSITY OF DHAKA
|
রিয়াদুস সালেহীন জাওয়াদ এই মুহূর্তে সারা বিশ্বের সকল সরকারের সামনে ভাবনার বিষয় দুইটিঃ নিজ দেশে করোনাভাইরাস পরিস্থিতি সামাল দেয়া এবং নিজেদের অর্থনীতিকে একটি অবশ্যম্ভাবী মন্দার জন্য প্রস্তুত করা। মন্দার প্রস্তুতি হিসেবে অনেক সরকারই বিভিন্ন কৌশল গ্রহণ করা শুরু করেছেন, জার্মানির অর্থমন্ত্রী ঘোষণা দিয়েছেন সরকারি ব্যয় কমানোর, যুক্তরাজ্যের মন্ত্রীও ইঙ্গিত করেছেন সেই দিকেই। যদিও এই ব্যয় সংকোচনের ফলাফল কী হবে সেটি এখনই বলা সম্ভব নয়, তবুও এর আগেরবারের উদাহরণ থেকে আমরা বেশ গুরুত্বপূর্ণ একটা শিক্ষা পেতে পারিঃ নব্যউদারবাদী নীতি কোনোভাবেই একটি জাতিকে একটি অতিমারীর সাথে লড়াই করবার জন্য তৈরী করতে পারে না। ১৯৮০ সালের পর থেকে পশ্চিমা বিশ্বে নব্যউদারবাদী নীতির জয়জয়কার চলেছিলো প্রায় বছর ত্রিশ। আটলান্টিকের দু’ ধারেই একটি স্বল্প ব্যয় করা সীমিত আকারের সরকারকে সাধারণ মানুষের জন্য ভালো ব্যবস্থা হিসেবে ধরে নেয়া হয়েছিলো। কিন্তু ২০০৮ এর বিশ্বমন্দা সেই দৃষ্টিভঙ্গির ভীত বেশ ভালোভাবেই নাড়িয়ে দিয়েছিলো। কিন্তু সরকারগুলো একদিকে যেমন ব্যাংক এবং কর্পোরেশনসমূহকে দেউলিয়াত্বের হাত থেকে বাঁচাতে বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার ঢালছিলো, তেমনি বাজেট ঘাটতি এবং জাতীয় ঋণের পরিমাণ কমাতে তারা সামাজিক সুরক্ষা, শিক্ষা, চিকিৎসা ইত্যাদি খাত থেকে বরাদ্দও হ্রাস করছিলো। এখন যখন সারা বিশ্বকে করোনাভাইরাসের সাথে যুদ্ধ করতে হচ্ছে, প্রায় ১২ বছর আগে নেয়া নব্যউদারবাদী নীতি ইউরোপকে আষ্টেপৃষ্ঠে বন্দি করে রেখেছে। প্রথমেই শুরু করা যাক ইউরোপের সবচেয়ে বেশি করোনা আক্রান্ত দেশ, স্পেনকে দিয়ে। ২০০৮ এর আগে স্পেনের স্বাস্থ্যব্যবস্থা ছিলো স্পেনের গর্বের বিষয়। কিন্তু ২০০৮ এ অর্থনৈতিক মন্দা শুরু হবার পর অন্যান্য অনেক দেশের মত জাপাতেরোর সরকার ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং আইএমএফ এর ব্যয়সংকোচনের ব্যবস্থাপত্র গ্রহণ করেন। বেকারত্বের হার যদিও পড়তির দিকে, গড়ে একটি স্প্যানিশ পরিবারের আয় ২০০৯ এর তুলনায় কমেছে ১৩%। শুধু তাই নয়, প্রায় ২০ লক্ষ স্প্যানিয়ার্ডের পক্ষে বাসস্থান পাওয়া সম্ভব হয় না, যার একটি বড় কারণ সরকারি আবাসন ব্যবস্থার অভাব। স্পেনের আবাসন ব্যবস্থার মাত্র ১% সরকারি ভর্তুকি পেয়ে থাকে, নেদারল্যান্ডে যেই সংখ্যাটি ৩২%। দারিদ্রের হারও বেড়েছে সমানতালে। ২০০৮-এ যেখানে ১.৭% মানুষ দারিদ্রের কবলে ছিলেন, ২০১৫ এর মধ্যে সেই হারটি দাঁড়িয়েছে ৩.২০%-এ। স্প্যানিশ শিশুদের মধ্যে ৩১.৩% দারিদ্রের ঝুঁকিতে বাস করে। সব মিলিয়ে স্পেনে তৈরি হয়েছে একটি ঝুঁকিপূর্ণ জনসংখ্যা। তবুও হয়ত স্পেনের পক্ষে মহামারীটি সামাল দেয়া সম্ভব হতো, যদি তাদের গর্বের স্বাস্থ্যব্যবস্থাটি অক্ষুণ্ণ থাকত। কিন্তু ২০১১ থেকে শুরু করে স্পেন স্বাস্থ্য এবং শিক্ষাখাতে প্রায় ১০ বিলিয়ন ইউরো বরাদ্দ কমিয়েছে। ২০০৯ এ স্পেনের জিডিপির ৬.৮% যেতো চিকিৎসা খাতে, সেই হারটি হমে এসেছে ৫.৯%-এ। এর ফলাফলও দেখা গিয়েছিলো বেশ প্রকটভাবেই। স্পেনের ডাক্তাররা চাকরির অভাবে দেশ ছেড়েছেন, অস্থায়ী চুক্তিতে কোনোরকম নিরাপত্তাছাড়া কাজ করতে বাধ্য হয়েছেন। হাসপাতালে পড়েছে আইসিইউর সংকট। প্রতি ১ লাখ মানুষের জন্য ইউরোপীয় ইউনিয়নে যখন ১১টি আইসিউ বিদ্যমান, স্পেনে সেই সংখ্যা ৯.৬৭টি। তার সাথে যোগ হয়েছে স্থানীয় পর্যায়ে স্বাস্থ্যব্যবস্থা বেসরকারিকরণের উদ্যোগ যা একটি অতিমারীর সময়কার সমন্বয়কে প্রায় অসম্ভব করে তুলেছে। তার ফলাফল হিসেবেই বিশ্বে করোনা আক্রান্তের সংখ্যায় স্পেনের অবস্থান দ্বিতীয়। স্পেনের অন্য যে প্রতিবেশির ওপর করোনাভাইরাসের একটি বিশাল ছাপ পরেছে তার নাম ইতালি। ২০০৮ এর পর থেকে একটি ধুঁকতে থাকা অর্থনীতিকে বাঁচাতে আইএমএফ এবং ইউরোপীয় ইউনিয়ন একের পর এক ব্যায়সংকোচনের কথা বলেছে এবং ইতালির সরকার সেটিকেই মান্য করে গেছে। কর্মসংস্থান ইতালিতে তৈরি হয়েছে যতসামান্যই, কিন্তু দারিদ্র্যের হার বেড়েছে ধারাবাহিকভাবে, সাত বছরে সেটি হয়েছে দ্বিগুণেরও বেশি। ব্যক্তিগত চরম দারিদ্র্যের হার বেড়েছে প্রায় আড়াই গুণ। এই সব কারণ এবং একটি বিশাল সংখ্যক বৃদ্ধ জনগোষ্ঠীর কারণে করোনাভাইরাসে মৃত্যুর দিক দিয়ে ইতালি পৃথিবীতে দ্বিতীয়। কিন্তু এই সবের পরেও অনেক মানুষের সত্যিকার কফিনে শেষ পেরেক ছিলো দেশের অর্থনীতিকে বাঁচানোর জন্য ১০ বছর ধরে প্রায় ৩৭ বিলিয়ন ইউরোর বরাদ্দ বাতিল। এবার বলা যাক কিছুটা ভিন্ন একটি গল্প, ব্রিটেনের গল্প। ব্রিটেনের স্বাস্থ্যসেবা বিশ্বের সেরা স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থাগুলোর মধ্যে অন্যতম। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরপরই ব্রিটেনে সার্বজনীন স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা শুরু হয়। ব্রিটেনের জাতীয় স্বাস্থ্য সেবা প্রায় ৮৫% সেবা প্রদান করে থাকে, বাকি ১৫% দেয়া হয় প্রাইভেট সেক্টরে, যদিও সেই প্রাইভেট সেক্টরও অনেক ক্ষেত্রে (সার্জারি এবং ক্যান্সার চিকিৎসা) জাতীয় স্বাস্থ্য সেবার উপর নির্ভরশীল। কিন্তু ২০০৮ এর বিশ্বমন্দার কারণে ব্রিটেনের রক্ষণশীল দল ডেভিড ক্যামেরুনের নেতৃত্বে ব্যয়সংকোচনের নীতি গ্রহণ করে। এর ফলাফল স্বরূপ প্রায় তিন লক্ষ বিশ হাজার মানুষ গৃহহীন হয়ে পরে, ১২ লক্ষ মানুষ খাবারের রেশনের উপর নির্ভরশীল হয়ে পরে এবং ১৩ লক্ষ দেউলিয়া হয়ে পরে। ব্রিটেনে যদিও বড় অংকের বরাদ্দ কমানো হয় নি, তবে চাহিদা অনুযায়ী বরাদ্দ বৃদ্ধি অনেকটাই কমিয়ে দেয়া হয়। সৃষ্টির শুরু থেকে জাতীয় স্বাস্থ্য সেবায় প্রতিবছর ৩.৭% হারে বরাদ্দ বাড়ানো হত। ২০০১/০২ থেকে ২০০৪/০৫ সালে বরাদ্দ বাড়ানো হয়েছিলো ৮.৬% হারে। কিন্তু ২০০৯/১০-২০১৮/১৯ এর মধ্যে বরাদ্দ বেড়েছে মাত্র ১.৪% হারে। অন্যদিকে ২০১৩/১৪-২০১৭/১৮ সালের মধ্যে স্থানীয় পর্যায়ে ব্যয় কমানো হয়েছে ৮%। এর ফলে স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে সরবরাহকারীদের হিমশিম খেতে হচ্ছে। ব্রিটেনে স্বাস্থ্য সেবার বরাদ্দের ব্যবস্থাপনা করে স্থানীয় কিছু ট্রাস্ট। ২০১০/১১ সালে এই ট্রাস্টগুলোর মাত্র ৫% তাদের বরাদ্দের চেয়ে বেশি টাকা খরচ করেছিলো, ২০১৮/১৯ এ বেশি খরচ করতে বাধ্য হওয়া ট্রাস্টের সংখ্যা ৪৮%। এর ফলে কমছে সেবা প্রদানের মানও। স্থানীয় পর্যায়ে চার ভাগের তিনভাগ নার্সই বলেছেন, তাদের সংখ্যা কম থাকায় হাসপাতালের অনেক প্রয়োজনীয় কাজও তারা সেরে উঠতে পারেন না। ব্রিটেন এখন তার মানুষকে বাঁচাতে একটি বছর মেয়াদী লকডাউনের কথা চিন্তাভাবনা করতে বাধ্য হচ্ছে। তবুও এই সব দেশে এবং বাংলাদেশে হাজার হাজার স্বাস্থ্যকর্মী নিজেদের ভবিষ্যতের কথা, স্বাস্থ্যের কথা চিন্তা না করে দিন রাত অক্লান্ত পরিশ্রম করছেন, অসম্ভব সব বাধাকে অতিক্রম করে মানুষের জীবন বাঁচাচ্ছেন। এই সকল স্বাস্থ্যকর্মীর জন্য নিরন্তর শুভকামনা।
0 Comments
Leave a Reply. |
Send your articles to: |